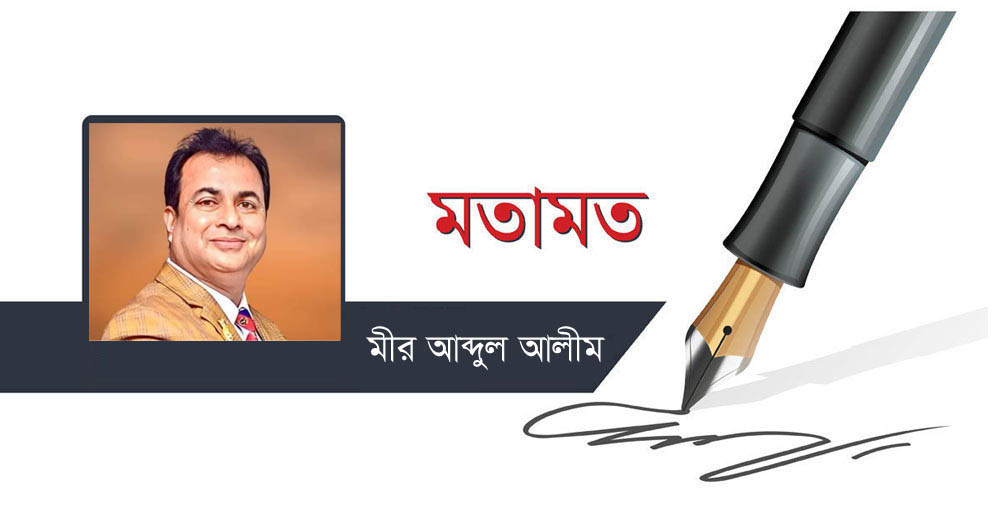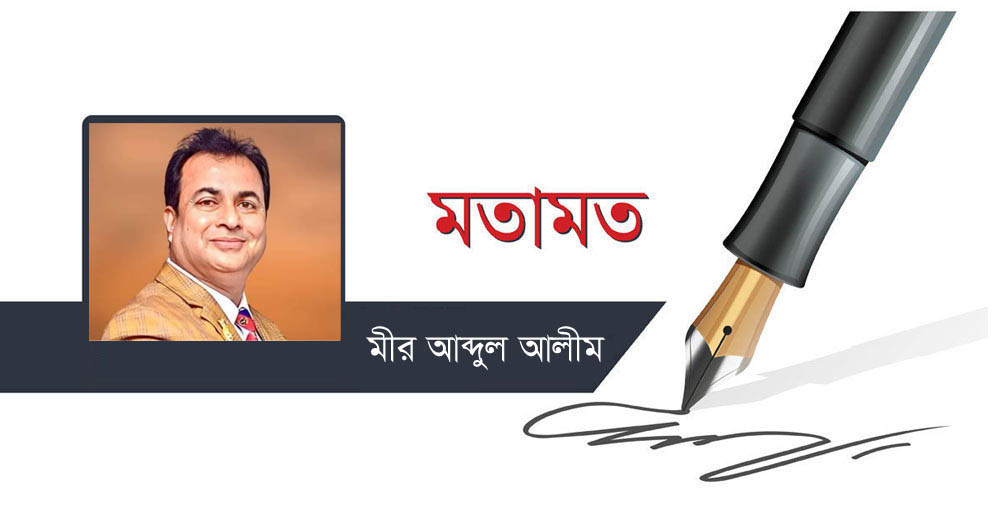ভূমি যখন কেঁপে ওঠে, তখন শুধু ঘর-বাড়ি, সেতু কিংবা বহুতল ভবন নড়ে না—নড়ে ওঠে মানুষের মনের গভীরে জমে থাকা হাজার বছরের আতঙ্ক। ভূমিকম্পের শব্দ অনেকটা এমন, যেন পৃথিবী হঠাৎ তার অন্তঃস্থলে জমে থাকা বেদনা এক নিঃশ্বাসে বের করে দেয়। একুশে নভেম্বরের সেই ভূমিকম্পও তেমনই ছিল। খুব বেশি মাত্রার না হলেও, উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতে হওয়ায় তার প্রভাব ছিল গভীর, এবং তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বড় কিছুর পূর্বাভাস।
এভাবে প্রতিটি কম্পন যেন আমাদের কানে ফিসফিস করে বলে—“সতর্ক হও, সময় আর বেশি নেই।”
এই লেখায় পয়েন্ট এর উপরে বাংলাদেশের ভূমিকম্প অবস্থার ওপর বিষদ আলোচনা করা হলো।
১. সাম্প্রতিক ভূমিকম্প:
নরসিংদীর মাটি কেঁপে ওঠা যে সতর্ক সংকেত-
২১ নভেম্বর ভোরে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের একটি কম্পনেই ঢাকার উচ্চ ভবনগুলো দুলে উঠল, হাসপাতালের রোগীরা আতঙ্কে ছুটে বেরিয়ে এল, মানুষ দৌড়ে নামল মাঠে। ঢাকার মতো জনসংখ্যা সঘন শহর যখন কেঁপে ওঠে, তখন আতঙ্কের মাত্রা বেড়ে যায় দশগুণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, উৎপত্তিস্থল যত কাছাকাছি, কম্পন তত বেশি তীব্র অনুভূত হয়। নরসিংদী-টাঙ্গাইল অঞ্চল বাংলাদেশের সক্রিয় ফল্ট লাইনের খুব কাছে। ফলে মাত্রা কম হলেও ধাক্কা বেশি অনুভূত হয়েছে। এ ভূমিকম্পে রাজধানীর বহু ভবনে ফাটল দেখা গেছে, দেয়াল ধসে পড়েছে। হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। কিছু এলাকায় গ্যাস লাইনে লিকেজের ঘটনা ঘটেছে, লিফট আটকে গেছে।
এগুলো বলছে- ঢাকা শহর প্রকৃত অর্থেই প্রস্তুত নয়।
এটাও প্রমাণ করল বাংলাদেশ আর “মধ্যম ঝুঁকির দেশ” নয়, বরং বড় ভূমিকম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হটস্পট।
২. গত ১০০ বছরের ভূমিকম্প ইতিহাস: বিপদ ছিল, এখন আরও কাছে।
বাংলাদেশ এবং এর আশপাশের অঞ্চলের শত বছরব্যাপী ভূমিকম্প ইতিহাস বলে এ অঞ্চল ভূমিকম্পকে প্রতিনিয়ত গর্ভে ধারণ করে আছে।
১৯১৮ সালের সিলেট ভূমিকম্প তখন সিলেট-আসাম অঞ্চলে হাজারো মানুষের মৃত্যু ঘটে। ১৯৩০ সালের ধুবরি ভূমিকম্প বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে। ১৯৫০ সালের আসাম ভূমিকম্প মাত্রা ছিল ৮.৬; পূর্ববঙ্গ কেঁপে উঠেছিল। ১৯৯৭ চট্টগ্রাম ভূমিকম্প পাহাড় ধসে বহু মানুষ মারা যায়।
২০১৫ নেপাল ভূমিকম্প বাংলাদেশে শতাধিক ভবনে ফাটল, বহু মৃত্যু, এবং ঢাকার সড়ক–ট্রাফিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
এছাড়া ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, বাংলাদেশের নিচে অন্তত পাঁচটি অত্যন্ত সক্রিয় ফল্ট লাইন আছে: ১. ডউকি ফল্ট, ২. সিলেট ফল্ট, ৩. চট্টগ্রাম টেকটনিক বেল্ট, ৪. মধুপুর ফল্ট, ৫. মিয়ানমার–বেঙ্গল সাবডাকশন জোন
এই সমস্ত ফল্ট লাইনে চাপ জমছে বহু বছর ধরে। কোনো একদিন এই চাপ “মেগা-থ্রাস্ট ভূমিকম্পে” রূপ নিতে পারে। এখনই আমরা সতর্ক না হলে প্রস্তুতি গ্রহণ না করলে হতাহতের সংখ্যা হাজার হাজার থাকবে। বাংলাদেশ পরিণত হতে পারে ধ্বংসস্তূপে।
৩. অপরিকল্পিত নগরায়ণ:
ঢাকাকে মৃত্যুফাঁদে পরিণত করেছে। ঢাকার জনসংখ্যা ২ কোটি ২০ লাখ। কিন্তু এই শহরের ভবনগুলো নির্মাণে সিসমিক কোড মানা হয়নি কমপক্ষে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে। প্রকৌশলীদের মতে,
অনেক ভবন “ফ্ল্যাট সিস্টেমে” তৈরি, যা ভূমিকম্প প্রতিরোধী নয়।
অনেক বহুতলের কলামে রড কম দেওয়া হয়েছে। রডে জং, নিম্নমানের সিমেন্ট–ইট, গাঁথুনিতে ফাঁক এসব ভবনকে ভূমিকম্পে অতি দুর্বল করে তোলে। ঢাকার মূল মাটি কাদামাটির, যা ভূমিকম্পের ঢেউ হাজার গুণ বাড়িয়ে দেয়। যাকে বলে “সয়েল অ্যামপ্লিফিকেশন”। এ অবস্থায় মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পেও ঢাকার বহুতল ভবনগুলো ডমিনোর মতো পড়ে যেতে পারে।
৪. স্বল্প বাজেট ও সরকারি প্রস্তুতির অভাব:
এই অবহেলার মূল্য ভয়ংকর হতে পারে। ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের বাজেট দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম। সরকার যেসব প্রকল্প নিয়েছে, তার অনেকই কাগজে আছে কিন্তু বাস্তবে নেই। এর প্রেক্ষিতে বলতে হয় ভূমিকম্পের ব্যাপারে সরকার উদাসীন। বিগত সরকারের সময়ও আমরা তাই দেখেছি। পুরনো ভবন অডিট করার প্রকল্প প্রায় স্থবির। রাজধানীর ভবনের সিসমিক মূল্যায়ন হয়নি ১০ শতাংশেও। উদ্ধারকার্যে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত আধুনিক যন্ত্র নেই। ফায়ার সার্ভিসের অনেক সদস্য ভূমিকম্প উদ্ধার মহড়ায় প্রশিক্ষিত নন। ভূমিকম্পের ব্যাপার রে প্রচার-প্রচারণা নেই বললেই চলে। জনসচেতনতার লক্ষ্যে কোন কার্যক্রম চোখে পড়ে না। বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন “যে দেশে বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা ৭২ শতাংশ, সেখানে দুর্যোগ বাজেট বাড়ানো বিলাসিতা নয়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন।”
৫. রাষ্ট্রের করণীয়:
এখনই সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতি হালনাগাদ জরুরি হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের করণীয়গুলো এখন আর বিকল্প নয়, বাধ্যতামূলক।
সিসমিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করতে হবে। রাজধানীর সব ভবনের বাধ্যতামূলক সিসমিক অডিট করতে হবে। পুরনো অবকাঠামো ভেঙে নতুন করে টেকসই ভবন নির্মাণ শুরু করতে হবে। ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, সিভিল ডিফেন্সকে আরও আধুনিক যন্ত্র, কাটা ধাতু সরানোর রোবট, থার্মাল স্ক্যানার দিতে হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এ না হলে বড় ভূমিকম্প হলে টিমব্যাকস বা জরুরি সরঞ্জাম আনতে সময় নষ্ট হবে এবং মানুষ মারা যাবে।
৬. অপরিকল্পিত ভবন:
দেশে সবচেয়ে বড় মৃত্যুফাঁদ পরিণত করেছে অপরিকল্পিত ভবন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঢাকার ২০,০০০ ভবন “অতি ঝুঁকিপূর্ণ” মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পেই ধসে পড়তে পারে। ভবন মালিকরা সিসমিক কোড অনুসরণ করছেন না, অনেক ঠিকাদার নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করছেন, ফলাফল ভয়ংকর।
আমরা ভুলে যাই ভূমিকম্প মানুষকে হত্যা করে না, হত্যা করে মানুষের তৈরি দুর্বল ভবন।
৭. বড় ভূমিকম্প হলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি:
সাত থেকে নয় মাত্রার ভূমিকম্প ভয়াবহতার হিসাব শিউরে ওঠার মতো হতে পারে। জাতিসংঘের বিশ্লেষণ, ঢাকায় যদি মাত্র ৭–৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয় ১–২ লক্ষ ভবন ধসে পড়বে। মৃত্যু হতে পারে ১–১.৫ লাখের বেশি মানুষ। ঢাকার হাসপাতাল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। ৩–৫ দিন উদ্ধারকাজে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। সড়ক ব্যবস্থায় যানজট এতই হবে যে অ্যাম্বুলেন্স চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়বে। গ্যাস লাইনে আগুন লাগার ঝুঁকি বিপুল। ব্যাংকিং, আইসিটি, টেলিকম, প্রশাসন সব অচল হয়ে যাবে। এই চিত্র কল্পনা নয়। এটাই হবে বাস্তবতা যদি এখনই প্রস্তুতি না নেওয়া হয়।
৮. বিশেষজ্ঞদের মতামত:
“এটা বড় ভূমিকম্পেরই পূর্বাভাস”: প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য “বাংলাদেশের নিচে ১০০ বছরের জমে থাকা চাপ এখন বিপজ্জনক স্তরে।”
“নরসিংদীর ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের ফর-শকও হতে পারে।” “মধুপুর ফল্ট যেকোনো সময় সক্রিয় হতে পারে। ঢাকার ওপর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি।” “মেগা-থ্রাস্ট ভূমিকম্প হলে ৮ মাত্রার উপরে যেতে পারে।”
দেশের শীর্ষ বিশেষজ্ঞরা এটাই বলছেন, সময়ের ব্যাপার মাত্র, প্রশ্ন হলো আমরা প্রস্তুত কি না।
৯. জনসচেতনতা: রাষ্ট্রের পরে সর্বোচ্চ অস্ত্র জনগণ।
ভূমিকম্পে সচেতন জনগোষ্ঠী হাজার প্রাণ বাঁচাতে পারে। বাংলাদেশে এখনো বেশিরভাগ মানুষ জানে না কোথায় আশ্রয় নিতে হবে। ভবনের সিঁড়ি কোথায় তা অনেকেই জানেন না। স্কুল–কলেজে ড্রিল হয় না। বাসা–অফিসে জরুরি ব্যাগ নেই। জনসচেতনতা বাড়াতে জরুরি, গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রচার, স্কুল–কলেজে ভূমিকম্প মহড়া বাধ্যতামূলক, কমিউনিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিটি অফিসে “Quick Response Team”, মোবাইল অ্যাপে সতর্কবার্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী।
১০. ভূমিকম্পের সময় করণীয়: মাথা রক্ষা করে টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন।
লিফট কখনো ব্যবহার করবেন না। বারান্দা, দরজা, জানালা থেকে দূরে থাকুন।
গ্যাস, বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিন।
খোলা জায়গায় থাকুন। ধসে যাওয়া এলাকা থেকে দূরে থাকুন। আতঙ্ক ছড়াবেন না, দৌড়াবেন না। এই সহজ নিয়মগুলোই হাজারো প্রাণ বাঁচাতে পারে।
১১. মিডিয়ার ভূমিকা:
ভূমিকম্পের সময়ে সংবাদমাধ্যমকে হতে হবে মানুষের চোখ, কান। তাদের ভূমিকা গুজব ঠেকানো, ভুল তথ্য না ছড়ানো, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ, উদ্ধার অভিযানে জনগণকে যুক্ত করা। বিশেষজ্ঞ মতামত তুলে ধরা
,করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, মিডিয়া যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন হতো, তবে আতঙ্কে মৃত্যু আরও বাড়বে।
১২. রাষ্ট্র, জনগণ ও গণমাধ্যম এই তিন শক্তি একসাথে দাঁড়ালে ক্ষতি কমবে: ভূমিকম্প ঠেকানো যায় না, কিন্তু ক্ষতি ঠেকানো যায়। এক্ষেত্রে তিন পক্ষকে একসাথে এগোতে হবে। রাষ্ট্র: নীতি, আইন, সরঞ্জাম, কঠোর ভবন নিয়ন্ত্রণ জনগণ: সচেতনতা, প্রস্তুতি, মিডিয়া তথ্য, নির্দেশনা, সতর্কতা এই তিন শক্তির ঐক্যই আমাদের রক্ষা করতে পারে।
উপসংহার:
আমরা আজ যে ফাটল দেখি, তা শুধু দেয়ালে নয়, এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায়, আমাদের নগরায়ণে, আমাদের সচেতনতার অভাবে।
দেয়াল ভেঙে গেলে নতুন করে গড়া যায়। কিন্তু মৃত্যু ফিরে আসে না। এখনই সময় এই কাঁপুনিকে সতর্কবার্তা হিসেবে গ্রহণ করার। যতদিন আমরা অব্যবস্থা, উদাসীনতা, অবহেলা ঢেকে রাখবো ততদিন এই মাটি আরও শক্তিশালী কম্পনের জন্য প্রস্তুত হবে।
আমরা কি প্রস্তুত হবো? নাকি ইতিহাস আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে,
“সতর্কবার্তা পেয়েও জাতি ঘুমিয়ে রইল”?
লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট। মহাসচিব- কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ