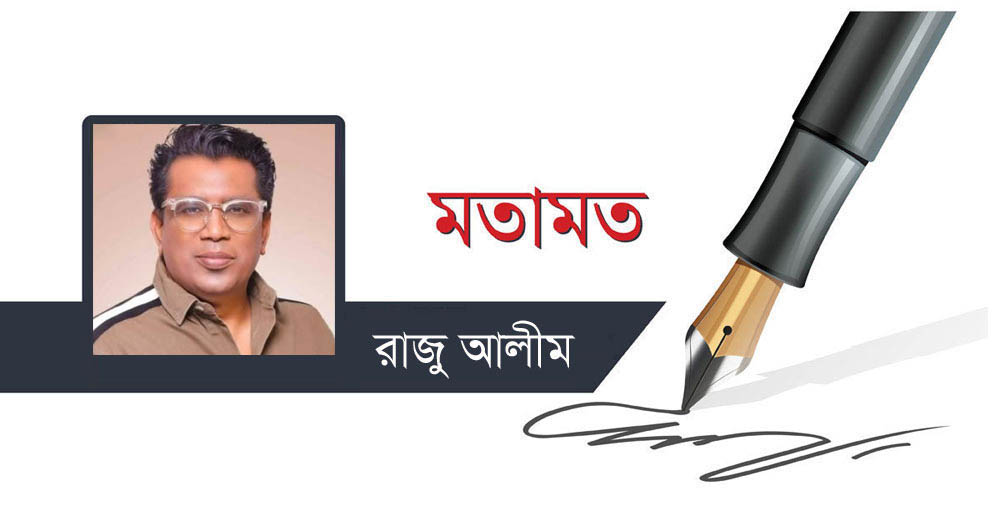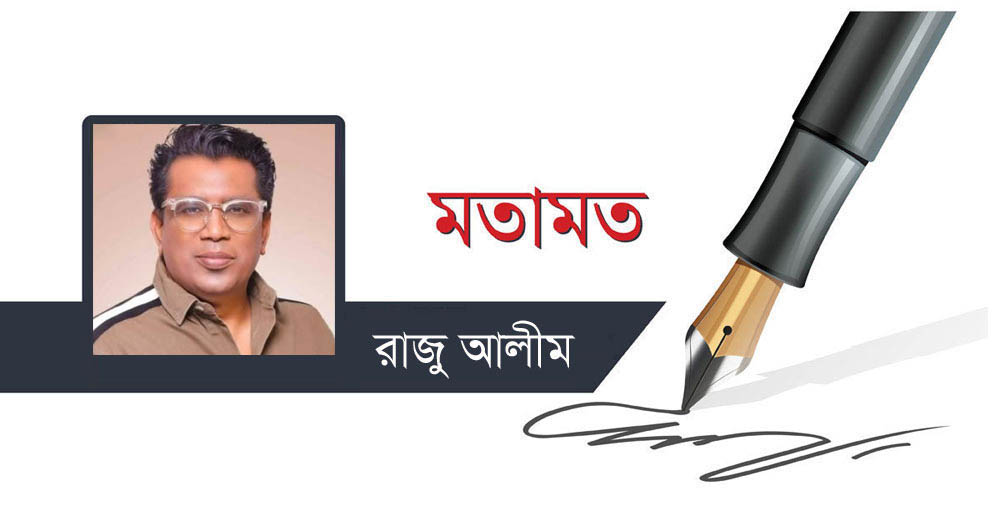বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় সবচেয়ে আলোচিত প্রশ্নগুলোর একটি হলো—ভারতের অবস্থান আসলে কোথায়? শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ঢাকার কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্য, আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার এবং নিরাপত্তা জোটের রাজনীতির সঙ্গে এই পরিবর্তনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের কার্যক্রম, বক্তব্য ও কূটনৈতিক আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে তারা এখনো আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক রাখার চেষ্টা করছে—অন্তত রাজনৈতিক পরিসরে একটি ভারসাম্য রক্ষার উপকরণ হিসেবে।
ভারতের এই অবস্থান নতুন কিছু নয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে দিল্লি আওয়ামী লীগকে তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক মিত্র হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। সীমান্ত নিরাপত্তা, জঙ্গিবাদ দমন, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর আশ্রয় নির্মূল এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে ভূমিকা রেখেছে, তা ভারত কখনোই অস্বীকার করেনি। বরং মোদির ভারত ও শেখ হাসিনার বাংলাদেশ এই পারস্পরিক সম্পর্ককে “গোল্ডেন এরা অব রিলেশনস” হিসেবে প্রচার করেছে। কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান এবং শেখ হাসিনার পতনের পর এই সম্পর্কের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেছে।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে রাজনৈতিক পুনর্গঠন ঘটছে, সেখানে ভারতের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই সীমিত হয়ে পড়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিষ্ঠা, সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, নতুন সংবিধান কমিশন সবকিছু মিলিয়ে ভারতের পুরোনো কূটনৈতিক কৌশল এখন কার্যত অচল। তাই দিল্লির কূটনীতিক ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নতুন বাস্তবতায় আওয়ামী লীগকে আবারও আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। তাদের যুক্তি হলো, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি, জামায়াত কিংবা বামপন্থী শক্তিগুলোর পুনরুত্থান ভারতের নিরাপত্তা ও সীমান্ত স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্যতা এখন তলানিতে। দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসন, দুর্নীতি, গুম-খুন, অর্থ পাচার, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ধ্বংস—সব মিলিয়ে এই দলটি জনআস্থা হারিয়েছে। জনগণের দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ এখন কেবল একটি পতিত ক্ষমতাসীন দল, যার ওপর বিদেশি সমর্থন ছাড়া কোনো রাজনৈতিক পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নেই। এমন প্রেক্ষাপটে ভারতের এই ‘প্রাসঙ্গিক রাখার চেষ্টা’ আসলে একধরনের কৌশলগত জেদ, যা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না।
ভারতের নীতিনির্ধারকদের কাছে আওয়ামী লীগ শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়; এটি তাদের নিরাপত্তা কৌশলের অংশ। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং’ ‘র’ এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বহুবারই উল্লেখ করেছেন যে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশের ভেতরে ভারতবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। দিল্লির দৃষ্টিতে সেটিই ছিল সবচেয়ে বড় অর্জন। কিন্তু এই যুক্তি যতই কূটনৈতিকভাবে শক্তিশালী হোক, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও জনগণের ইচ্ছার বিপরীতে অবস্থান নেওয়া ভারতের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এখন ভারতের ভূমিকা নিয়ে স্পষ্টতই সমালোচনামুখর।
ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নতুন ধারা, বিশেষ করে নেইবার ফার্স্ট ও পলিটিক্স এর আলোকে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূখণ্ড। তাই দিল্লি কোনো অবস্থাতেই চায় না যে ঢাকা সম্পূর্ণভাবে অন্য কোনো প্রভাববলয়ে চলে যাক। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ, চীনের অবকাঠামোগত বিনিয়োগ এবং উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রভাব, সবকিছুই ভারতকে চিন্তায় ফেলেছে। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক রাখার চেষ্টা আসলে ভারতের নিজস্ব ভয়েরই প্রতিফলন, যেখানে তারা মনে করছে যে বিকল্প কোনো সরকার তাদের কৌশলগত স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল নাও হতে পারে।
তবে ভারত জানে, পরিস্থিতি বদলে গেছে। শেখ হাসিনার প্রতি দীর্ঘ সমর্থন দিল্লির জন্য এখন একধরনের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন বাংলাদেশে যেখানে অন্তর্বর্তী সরকার জনপ্রিয়তার ওপর দাঁড়িয়ে সংস্কারের পথে অগ্রসর হচ্ছে, সেখানে ভারত যদি আওয়ামী লীগকেন্দ্রিক রাজনীতির ওপর বেশি নির্ভর করে, তবে তা তারই কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে। তাই ভারতের নতুন কৌশল হলো, আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক মঞ্চে রাখার পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ বজায় রাখা। এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতের ক্ষমতার ভারসাম্যে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে চায়।
এই কৌশল কতটা সফল হবে, তা এখনই বলা কঠিন। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোর অবস্থান ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তারা বিদেশি হস্তক্ষেপকে ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন এই সরকার বুঝতে পারছে যে, জনগণের মধ্যে বিদেশি প্রভাব নিয়ে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে। তাই তারা যদি ভারতের প্রতি অতিরিক্ত নমনীয়তা দেখায়, তবে তা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ফলে দিল্লির জন্য বর্তমান পরিস্থিতি একধরনের ‘ডিপ্লোম্যাটিক ট্রায়াল’।
ভারতের ভেতরেও এই নীতির বিরোধিতা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাবেক কূটনীতিক স্পষ্টভাবে বলেছেন, শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের নতুন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ভারতের উচিত ‘নিউট্রাল এঙ্গেজমেন্ট’ নীতি গ্রহণ করা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কৌশল এখনো আওয়ামী লীগকেন্দ্রিক; তারা মনে করছে যে এই দলটি ছাড়া বাংলাদেশে স্থিতিশীল গণতন্ত্র টিকবে না। এ ধরনের চিন্তাধারা কেবল অযৌক্তিকই নয়, বরং বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক রায়কে অসম্মান করার শামিল।
বাংলাদেশের তরুণ সমাজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি এখন রাজনীতিতে নতুন বিকল্পের খোঁজ করছে। তারা দলীয় রাজনীতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনকে। এই পরিবর্তনের স্রোতকে অবজ্ঞা করে যদি ভারত কেবল পুরনো রাজনৈতিক মিত্রের পুনরুত্থান চায়, তবে তা ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ককে অস্থির করে তুলতে পারে। ভারতের উচিত হবে, বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা—দল নয়, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা।
অবশেষে বলা যায়, আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক রাখার ভারতের এই চেষ্টা কেবল কূটনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল নয়, এটি বাস্তবতাবিরোধীও। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন নতুন ভারসাম্য তৈরি হচ্ছে, যেখানে জনগণের ইচ্ছাই সবচেয়ে বড় নিয়ামক। ভারত যদি এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বহু বছরের আঞ্চলিক প্রভাবও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। এখন সময় এসেছে, দিল্লি বুঝে নিক—বাংলাদেশে কোনো দল নয়, জনগণই ভবিষ্যতের রাজনীতির একমাত্র শক্তি।
ভারতের কূটনৈতিক অঙ্গনে এখন মূল প্রশ্ন হলো—বাংলাদেশে তাদের দীর্ঘদিনের বিনিয়োগ করা রাজনৈতিক পুঁজি কতটা টিকিয়ে রাখা সম্ভব? শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দিল্লি শুধু একটি বন্ধু হারায়নি, হারিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের এক ধরনের ‘স্ট্র্যাটেজিক কমফোর্ট জোন’। বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনীতিতে নতুন শক্তিগুলোর উত্থান, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে যে নতুন গণআন্দোলনের বীজ বপন হয়েছে, তা ভারতের প্রচলিত ‘স্টেট-টু-পার্টি’ সম্পর্ক মডেলকে চ্যালেঞ্জ করছে। ফলে দিল্লি এখন এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি—যেখানে কোনো দল নয়, জনগণই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের প্রধান নিয়ামক।
ভারতের জন্য এই পরিবর্তনটি অস্বস্তিকর। কারণ গত দেড় দশক ধরে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে দলীয় নেতৃত্বকেন্দ্রিক মডেলে। শেখ হাসিনা ছিলেন সেই মডেলের কেন্দ্রবিন্দু। তার মাধ্যমে তারা ঢাকায় প্রভাব বিস্তার করেছে, সীমান্তনীতি নির্ধারণে সুবিধা পেয়েছে, এমনকি আঞ্চলিক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ সুবিধাও ভোগ করেছে। কিন্তু এখন সেই ‘বিশ্বস্ত সেতুবন্ধন’ আর নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের নীতিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে—তারা বিদেশি প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চায় এবং প্রতিটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আনতে আগ্রহী। এই নীতির ফলে ভারতের জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে আগের মতো একচেটিয়া সুবিধা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।
অন্যদিকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চিত্রও বদলাচ্ছে। বিএনপি ও নাগরিক সমাজের নেতৃত্বে যে নতুন রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠছে, তা ভারতের পুরোনো আশঙ্কাগুলোকে অকার্যকর করে দিচ্ছে। কারণ এই নতুন জোট ভারতবিরোধী নয়; বরং তারা আঞ্চলিক ভারসাম্য, পারস্পরিক সম্মান ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী। দিল্লি যদি এই পরিবর্তনকে সুযোগ হিসেবে নিতে পারে, তবে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও সমতাভিত্তিক হতে পারে। কিন্তু যদি তারা পুরোনো ধ্যানধারণা আঁকড়ে থাকে—যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগই ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম—তবে তা হবে এক ভয়াবহ কূটনৈতিক ভুল।
বাংলাদেশের ভেতরে আজ যে ‘রাজনৈতিক রিসেট’ ঘটছে, তার মূল চালিকাশক্তি জনগণ। সেনানির্ভর অন্তর্বর্তী সরকারও বুঝতে পারছে যে তাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে জনগণের আস্থার ওপর, বিদেশি মদতের ওপর নয়। ভারত যদি সত্যিই বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা চায়, তবে তাদের উচিত হবে জনগণের এই রাজনৈতিক রায়কে সম্মান করা। এখন আর সময় নয় পুরোনো বন্ধু বাঁচানোর; সময় এসেছে নতুন বাস্তবতায় নতুন বন্ধুত্ব গড়ে তোলার। বাংলাদেশের রাজনীতি যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, তেমনি দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতেও নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভারতের ভূমিকা নির্ভর করবে—তারা কি জনগণনির্ভর বাংলাদেশকে গ্রহণ করবে, নাকি অতীতের ব্যর্থ কৌশলে আবদ্ধ থাকবে।
লেখক: কবি, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।